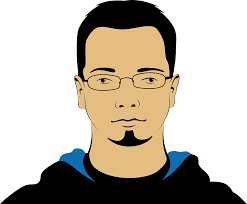

আকাশ মো. জসিম। ২২ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।
রাষ্ট্রে সামাজিক ও ন্যায় বিচার ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার জন্যে রাজনৈতিক শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার মানদন্ড প্রতিষ্ঠা খুবই জরুরী। সুশাসনের মূলে থাকে জবাবদিহিতা। জনগণের যদি সরকারের ওপর আস্থা থাকে বা তারা যদি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সরকারের জবাবদিহির যে মৌলিক ধাপগুলো আছে, তার প্রথমটা পূরণ হয়ে যায়।
আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সরকার তো জনগণের। জনগণের রায়ের ওপর ভিত্তি করে জনগণ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কাজ করে। তাই জন আস্থার বিষয়টা প্রথমেই আসে। সামনের দিনগুলোতে দেখতে হবে নীতিকাঠামো, আইন ও প্রতিষ্ঠানগুলোয় জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন কতটুকু ঘটছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নীতিকাঠামো, আইনিকাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের কাছে কতটুকু জবাবদিহিমূলক হলো।
সুশাসনের বিষয়টা শুধু এই নির্বাচনের ওপর নির্ভরশীল নয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটা শাসনকাঠামো তৈরি হয়েছে। জবাবদিহির জন্য যে মৌলিক উপাদানগুলো থাকার কথা, সেগুলো কাগজে-কলমে আছে। কিন্তু সেগুলোর কার্যকারিতা খুবই দুর্বল। এর সঙ্গে এখন নতুন যে আরেকটি উপাদান যোগ হলো, তা হলো শাসনকাঠামোটা একচ্ছত্র হয়ে গেছে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।
যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের সিংহভাগ ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী, যাঁরা স্বতন্ত্র, তাঁরাও ক্ষমতাসীন দলের সদস্য। তাঁদের পরিচিতি, রাজনীতি সবই হলো ক্ষমতাসীন দলের। আরও যাঁরা আছেন, তাঁরাও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকগোষ্ঠী। অল্প কিছু আছেন, যাঁরা এর বাইরে।
সংসদের বিশাল অংশ যদি একটি দলের করায়ত্ত হয়, তখন শাসনকাঠামো একচ্ছত্র না বলে আর উপায় থাকে না। সরকারি কার্যক্রমে জনপ্রত্যাশা কতখানি প্রতিফলিত হবে, তার আগে যে বিষয়টি আসল, তা হলো জবাবদিহির কোনো কাঠামোই আর থাকল না।
সংসদের কথা যদি বলি, সংসদ তখনই কাজ করে, যখন জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকে। তা ছাড়া তার কাজ আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগণের পক্ষ হয়ে সরকারকে জবাবদিহি করা।
এই তিনটি কাজের কোনোটিই বাস্তবে হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, এই সংসদে চেকস অ্যান্ড ব্যালান্স বলতে যেটা বোঝায়, সেটা অনুপস্থিত থাকবে। সংসদের সফলতা নির্ভর করবে যদি দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ওঠে সংসদ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন। এটা আমরা শুধু আশাই করতে পারি, আদৌ সম্ভাবনা কতটুকু তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাবে।
নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে গবেষণা করেছে। আগের দুটি নির্বাচনেও তারা পরিবীক্ষণ বা ট্র্যাকিং করেছে। তারা আলাদাভাবে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বসেছিল। নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিকভাবে সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার এখতিয়ার আছে।
আর সরকারসহ সব প্রতিষ্ঠানের কমিশনকে সহযোগিতা করার আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে। আগের দুই নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিয়ে সংকট দেখা গিয়েছিল।
এবার এই সংকট আরও প্রকট হয়েছে। বিএনপি যেটা বলছে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ধারণা, আমাদের সেদিকে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। নির্বাচনকালীন সরকারকে আমরা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তার ভূমিকাকে নিরপেক্ষ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত করা নিশ্চিত করা যায়। যে যে কারণে সরকারের পক্ষে নিরপেক্ষ বা স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত হওয়া সম্ভব নয় বা যে যে কারণে আস্থা সৃষ্টি করা যাচ্ছে না, সেগুলো চিহ্নিত করে কমিশন কিছু আইনি পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রস্তাব তুলতে পারত।
কমিশন যদি এটা করত, অন্তত তাদের মনে এই আত্মবিশ্বাসটা জন্মাত যে তাদের কাছে মানুষের যে প্রত্যাশা, সেটা তারা পূরণ করতে পারল।
টিআইবি সরাসরি তাদের সঙ্গে দেখা করেছে। এই সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলো তাদের কাছে দিয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এই প্রস্তাবগুলো যুক্তিযুক্ত, এগুলো উপস্থাপন করতে পারবে কি না, সেটা তারা বিবেচনা করবে। তারা সেটা করেনি। শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময় বিতর্কিত এবং বিপরীতমুখী ভূমিকা রেখেছে।
নির্বাচন সামনে রেখে কমিশন যে চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করেছিল, তাতে ১ নম্বর ছিল বিরোধী দলকে নির্বাচনে আনা। যখন তাদের সামনে এই চ্যালেঞ্জ, তখন তাদের কী করা উচিত ছিল ? তাদের উচিত ছিল নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা। এই সুযোগ তারা নেয়নি বা এড়িয়ে গেছে। তারা বাধ্যবাধকতার যুক্তি দেখিয়েছে। কখনো বলেছে বিকল্প তাদের হাতে ছিল না। আমরা বলতে চাই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল, তারা কাজে লাগায়নি।
কেন করল না, সেই উত্তর নির্বাচন কমিশন দিতে পারবে। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে বিতর্কিত কিছু সংশোধনী এসেছে। তারপরও সার্বিকভাবে সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, সেটি যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য যে সৎ সাহস, মনোবল দরকার, সেটিও আমরা দেখতে পাইনি। হয়তো কোনো কারণে তারা চাপের মধ্যে ছিল। তার কিছু কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। সে কারণে কমিশন হয়তো নিজেদের ক্ষমতাহীন ভেবেছে। কিন্তু সেটা তারা স্বীকার করতে চায়নি। দায়টা কমিশন নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছে।
আইনগতভাবে নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনামার মাধ্যমে যে তথ্য দেয়া হয়েছে, তা যদি অপর্যাপ্ত বা ভুল তথ্য হয়, তথ্য গোপন বা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত আয় যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল হওয়ার আইনগত বিধান রয়েছে। নির্বাচনের আগে ব্যবস্থা নেয়া সহজ, তবে নির্বাচনের পরও কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে একা নির্বাচন কমিশন এই কাজ করতে পারে না, তার সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে যুক্ত হতে হয়।
যেকোনো পেশা হোক, ব্যবসায়ী, অভিনেতা বা খেলোয়াড় প্রত্যেকের কিন্তু রাজনীতিতে অংশ নেয়ার অধিকার আছে। এখানে কেউ বাধা দেবে না। আমাদের প্রশ্ন করারও কোনো সুযোগ নেই।
দেখার বিষয় হলো বিশ্বব্যাপী যে গণতান্ত্রিক চর্চা তাঁরা কি সেই চর্চা করে রাজনীতিতে আসছেন, নাকি তাঁরা সরাসরি দলের মনোনয়ন পেয়ে যাচ্ছেন। এবার যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের ৬৫ শতাংশ ব্যবসায়ী। এঁদের বড় অংশ রাজনীতি না করেই এসেছেন। অনেকেই আছেন রাজনীতিক, যাঁর মূল পেশা ব্যবসায়ী। সেটা হতেই পারে। এর বাইরে অনুপ্রবেশ শব্দটা যদি ব্যবহার করি…। আমরা বলতে চাইছি স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অনেকেই আসছেন না।
নির্বাচন কমিশনের ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দেয়া উচিত। ২০১৮ সালের তুলনায় ব্যয় কিছু বাড়বে। পাঁচ বছর আগের তুলনায় সবকিছুর দাম বেড়েছে। কিন্তু খরচের তো সীমা আছে। দেখা যাচ্ছে খরচ তিন গুণ বেড়েছে। হিসেব এখনো চলমান। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দায় আছে কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে, সেটা প্রকাশ করার।
যে আসনগুলো টিআইবির গবেষণার আওতায় এসেছে, সেখান থেকে আমরা তথ্যগুলো পেয়েছি। এর সঙ্গে গণমাধ্যমের তথ্য মিলে গেছে। যেটা হয়েছে, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের দিক থেকেও বলা হয়েছে ভোটার উপস্থিতি জরুরি। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের অর্থ দাঁড় করানো হয়েছিল ভোটারদের অংশগ্রহণ। সেই হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে ৫০ শতাংশ ভোটার আনতে হবে এমন টার্গেট করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন অবশ্য বলেছিল, ১ শতাংশ ভোট পড়লেও বৈধতার কোনো সমস্যা নেই। সরকারি কর্মচারীদের অনেকেই স্বপ্রণোদিত হয়ে, কেউ অনানুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশিত হয়ে ভোটকেন্দ্রে গেছেন। আবার অনেককে বলা হয়েছে সেবা পাবেন না। সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের আওতায় যাঁরা আছেন, তাঁদের ভাতা বঞ্চিত করা হবে, এমন হুমকিও দেয়া হয়েছে।
গত এক-দেড় দশকে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে। আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা প্রশংসিত হয়েছি। কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে ধরুন, আমাদের জাতীয় আয় ৭ শতাংশ হিসেবে বাড়ছে।
সরকারের ঘোষিত তথ্য হচ্ছে, আমরা যদি মধ্যম পর্যায়েও দুর্নীতি রোধ করতে পারতাম, তাহলে আমাদের আয় আরও ৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ত। মানে আমাদের প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশ হতো। দুর্নীতির যে আর্থসামাজিক প্রভাব, সেটা আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। কিন্তু আমরা দেখি না। দুর্নীতির মধ্যেই একটা অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক উপাদান আছে।
সাধারণত মানুষকে তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে যে রোগটি, সেটি হলো দুর্নীতি। শুধু যদি সেবা খাতের দুর্নীতির কথা বলি, সেবা নিতে গিয়ে যাঁরা ব্যর্থ হন, টিআইবির জরিপে তাঁদের ৭৪ শতাংশ বলেন, তাঁরা ঘুষ দিতে না পারলে সেবা পান না।
যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর কথা। বললেন, আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী। সংবিধান পড়ি। সংবিধান আমার মুখস্থ। কিন্তু সংবিধানের মধ্যে তো আমি আমার নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না। তরুণেরা পরিবর্তন চান। তাঁরা বলে দুর্নীতি রোধ তাঁদের জন্য দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ।
লেখক : সম্পাদক ও প্রকাশক।
Leave a Reply